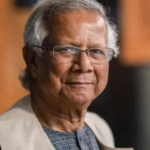We also contacted the Daily Nobojug but have not yet heard back from them although we noticed that they have published a short response to the reports of this case having been filed against them. In this response, they attempted to justify their position and their right to publish critical comments on the current government and issued a warning that if this kind of lawsuit persisted, free and fair journalism would be eradicated soon.
Category: বিশেষ সংবাদ
নির্যাতন রোধের হেল্পলাইনে করোনা নিয়ে ৯০% কল
নাটোরের গুরুদাসপুরে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইনে (১০৯ নম্বর) ফোন করে নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দেয়। এ ঘটনা চলতি বছরের শুরুর দিকে। মেয়েটি ফোন করার পর হেল্পলাইন থেকে তথ্য পাঠানো হয় গুরুদাসপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. তমাল হোসেনের কাছে। তিনি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে মেয়েটির বাড়িতে পাঠিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন।
শুধু বাল্যবিবাহ নয়, যেকোনো ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে হেল্পলাইনটি চালু করে। তবে চলতি বছর এতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধবিষয়ক কলের বদলে করোনা নিয়ে জানতে বেশি ফোন আসছে।

হেল্পলাইনটি পরিচালিত হয় মন্ত্রণালয়ের নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায়। তাদের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১১ লাখ ১৯ হাজারের মতো কল আসে। এর মধ্যে মাত্র ১ লাখ ১৯ হাজার কল আসে সাধারণ চিকিৎসা, পরামর্শ, পুলিশি সহায়তা, আইনি সহায়তা ও তথ্য চেয়ে। বাকি কলগুলোকে অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত করা হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, কিছু বাদ দিয়ে অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত কলগুলো মূলত করোনা নিয়ে। ১০ মাসে সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ে জানতে ১ হাজার ৭৩৭, পরামর্শ সেবা পেতে ৫৭৯, পুলিশি সহায়তা পেতে ১১ হাজার ৫৭৯, আইনি সহায়তা পেতে ১৮ হাজার ৫৬৮ এবং তথ্য পেতে ৮৬ হাজার ৬৭১টি কল আসে।
বিগত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা যায়, সাধারণত অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত কলের সংখ্যা খুব কম থাকে। যেমন ২০১৯ সালেও ১৮ লাখের মধ্যে ২৪ হাজারের মতো কল ছিল অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত। এবার মোট কলের ৯০ শতাংশই অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত। এ বিষয়ে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম প্রকল্পের পরিচালক আবুল হোসেন বলেন, এ বছর মানুষের করোনা নিয়ে উদ্বেগ বেশি ছিল। তাই এ হেল্পলাইনে করোনা নিয়েই ফোন বেশি এসেছে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে যখন হেল্পলাইনটি চালু করে, তখন নম্বর ছিল ১০৯২১। ২০১৭ সাল থেকে এটি ১০৯ নম্বরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে এটি টোল ফ্রি, অর্থাৎ বিনা মূল্যে কল করা যায়।
কর্মকর্তারা জানান, হেল্পলাইনটিতে তিন পালায় (শিফট) ২৪ ঘণ্টা ৭৮ জন কর্মী সেবা দেন। তবে গত আগস্টে জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ২৪ ঘণ্টা সেবা না পাওয়ার অভিযোগ করেন কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ। তিনি বলেন, গত ২৪ আগস্ট রাজধানীর শ্যামলীর এক নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে উদ্ধার পেতে ১০৯ নম্বরে বারবার ফোন করেও সাড়া পাননি। এ বিষয়ে মেহের আফরোজ প্রথম আলোকে বলেন, হেল্পলাইনে জনবল কম। পরিসর আরও বাড়াতে হবে।
বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা জানতে ১০৯ নম্বরে গত ২৪ নভেম্বর সকাল সাতটা ও বিকেল চারটায় দুবার প্রথম আলোর পক্ষ থেকে কল করা হয়। দুবারই কল ধরেন কর্মীরা। এর মধ্যে সকাল সাতটায় মো. রাসেল হোসেন নামের একজন কর্মী কল ধরেন। রাসেল বলেন, তিনি রাতের পালায় ৪৫টি কল ধরেছেন। এর মধ্যে মধ্যরাতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও যশোর থেকে নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে তিন নারী ফোন করেন। তিনটি ক্ষেত্রেই অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।
অবশ্য নারীদের অনেকেই সরকারের এ হেল্পলাইন সম্পর্কে জানেন না। সাতক্ষীরা জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির প্রধান সাকিবুর রহমান বলেন, এটি নিয়ে আরও প্রচার দরকার।
নিয়োগ ১০ বছর আগে, উন্নতি নেই কর্মক্ষেত্রে
‘সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা’—এই নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করতে ১০ বছর আগে অ্যাডহক ভিত্তিতে দুই দফায় ৪ হাজার ১৩৩ জন চিকিৎসককে (সহকারী সার্জন) নিয়োগ দিয়েছিল সরকার। এরপর গড়িয়েছে অনেক সময়, কিন্তু পরিবর্তন আসেনি এসব চিকিৎসকের ভাগ্যে। এই চিকিৎসকেরা ২০১০ সালে যে বেতনে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন, সেই স্কেলে বেতন পাচ্ছেন এখনো।
এই দীর্ঘ সময়ে তাঁদের চাকরি ক্যাডারভুক্ত করা হয়নি, হয়নি পদোন্নতিও। হতাশ হয়ে কেউ কেউ চলে গেছেন অন্য পেশায়।
এসব অনেক দিনের সমস্যা। আমরা এটা দূর করার চেষ্টা করছি। সমাধান হবে। তবে একটু সময় প্রয়োজন
মো. আবদুল মান্নান , স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব
এই চিকিৎসকদের কয়েকজন প্রথম আলোকে বলেন, বছরের পর বছর ধরে একই পদে থাকায় তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। চাকরির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ হওয়ার পরও বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকেরা পদোন্নতি পেয়ে তাঁদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা এফসিপিএস, এমডি, এমএস, এফআরসিএসের মতো উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও কর্মক্ষেত্রে এগোতে পারেননি।
৪ হাজার ১৩৩ জন চিকিৎসকের মধ্যে এখন কর্মরত আছেন ১ হাজার ৯৮৬ জন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অ্যাডহক কর্মকর্তাদের ক্যাডারভুক্ত করার বিষয়ে একটি প্রস্তাব গত সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে আর কোনো বাধা থাকবে না।
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, ‘এসব অনেক দিনের সমস্যা। আমরা এটা দূর করার চেষ্টা করছি। সমাধান হবে। তবে একটু সময় প্রয়োজন।’
নিয়োগ পেয়েছিলেন ৪ হাজার ১৩৩ জন চিকিৎসক। এখন চাকরিতে আছেন ১ হাজার ৯৮৬ জন।
প্রেক্ষাপট
২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইউনিয়ন পর্যায়ের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক–সংকট ছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র থেকে জানা গেছে, তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক ২০০৯ সালের ১৩ এপ্রিলের এক সভায় জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসকের পদ শূন্য। এত বিপুলসংখ্যক পদ খালি থাকায় জনগণের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। সে সময় জনপ্রতিনিধিরাও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। অনেকেই সংসদ অধিবেশনে নতুন চিকিৎসক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।
এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৮ জুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এবং একই বছরের ২৮ জুন তৎকালীন জনপ্রশাসন উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের কাছে আধা সরকারিপত্র পাঠান। সেখানে তিনি চিকিৎসক–সংকটের কথা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ৪ হাজার ১৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু সরকারি কর্ম কমিশন বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন নিয়োগের বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে অ্যাডহক ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। ২০১০ ও ২০১১ সালে ওই সংখ্যক চিকিৎসককে নিয়োগ দেওয়া হয়।
হতাশা
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নিয়োগ দেওয়ার পর এসব চিকিৎসককে পদায়ন করা হয়েছিল নিজ জেলা কিংবা আশপাশের উপজেলা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এসব চিকিৎসকের ভাষ্য, ২০১০-১১ সালে তাঁরা মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের ‘ত্যাগের’ মূল্যায়ন করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে তাঁদের অনেকেই ‘পড়াশোনাসহ নানা কারণে’ ঢাকায় চলে আসেন।
অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া অন্তত ৫০ জন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। চাকরিবিধি এবং পে স্কেল অনুযায়ী তাঁদের সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হয়নি।
চিকিৎসকেরা জানান, তাঁদের মধ্যে অন্তত এক হাজার চিকিৎসক উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। প্রায় ২০ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। ৭০ জন সাফল্যের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। গত ৩১ জুন তাঁদের নিয়োগের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু চাকরি নিয়মিত হলেও ক্যাডারভুক্ত না হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তাঁদের পরে যোগ দেওয়া ৩৩তম বিসিএসের চিকিৎসকেরা ষষ্ঠ গ্রেড পেয়েছেন। আর তাঁরা আছেন নবম গ্রেডেই। অনেকের বয়স শেষ হয়ে যাওয়ায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি।
চিকিৎসকদের ভাষ্য, প্রধানমন্ত্রী অ্যাডহক চিকিৎসকদের ক্যাডারভুক্ত করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে দেন। কমিটিকে বলা হয়েছিল, ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁরা এখনো কোনো অগ্রগতি দেখছেন না।
আমাদের অনেকেই ভারপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু আমাদের ভারমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার
মোহাম্মদ সায়েমুল হুদা, সাভারের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকদের একজন জাতীয় পুষ্টিসেবার উপব্যবস্থাপক নন্দলাল সূত্রধর প্রথম আলোকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকার পরও তাঁদের স্থায়ী না করা ও পদোন্নতি না দেওয়া দুঃখজনক। সাভারের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ সায়েমুল হুদা বলেন, ‘আমাদের অনেকেই ভারপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু আমাদের ভারমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।’
অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ক্যাডারভুক্ত ও পদোন্নতির জন্য অনেক দিন ধরে কাজ করছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব শারমিন আক্তার জাহান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদ প্রায় ১০ বছর। ক্যাডারভুক্ত না হওয়ায় তাঁরা সবাই প্রারম্ভিক স্কেলে বেতন তুলছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁরা কোনো পদোন্নতি পাননি।
শারমিন আক্তার জাহান জানান, ক্যাডার–বহির্ভূত অস্থায়ী কর্মকর্তাদের ক্যাডারভুক্ত করার বিষয়ে একটি প্রস্তাব গত সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে আর বাধা থাকবে না।
একজন চিকিৎসকের ১০ বছর পদোন্নতি না হলে তাঁর কি চাকরিতে আগ্রহ থাকে? স্বাস্থ্যসেবা বিভাগকে আমরা বারবার অনুরোধ করেছি সমস্যাটি সমাধান করতে
মো. ইহতেশামুল হক চৌধুরী , বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব
‘বারবার অনুরোধ করেছি’
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব মো. ইহতেশামুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারই তাঁদের নিয়োগ দিয়েছিল। তাঁরা তো জোর করে চাকরি নেননি। সে সময় তাঁরা মাঠপর্যায়ে যে সেবা দিয়েছেন, তা সবারই জানা। তখন বলা হয়েছিল, তাঁদের ক্যাডারভুক্ত করা হবে। আর পদোন্নতি তো নিয়মতান্ত্রিকভাবে হওয়ার কথা। এখন তাহলে কেন তাঁদের পদোন্নতি আটকে দেওয়া হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘একজন চিকিৎসকের ১০ বছর পদোন্নতি না হলে তাঁর কি চাকরিতে আগ্রহ থাকে? স্বাস্থ্যসেবা বিভাগকে আমরা বারবার অনুরোধ করেছি সমস্যাটি সমাধান করতে।’
শীতের শুরুতেই হাসপাতালে ভিড়
ঢাকায় কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) শয্যা জোগাড় করতে রোগীর স্বজনদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হাসপাতালগুলোর প্রায় সব আইসিইউ শয্যাই ভর্তি। সাধারণ শয্যাগুলোতেও রোগী বেড়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় করোনার জন্য নির্ধারিত সরকারি ব্যবস্থাপনার ৯টি হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা রয়েছে ১১৩টি। গতকাল মঙ্গলবার ৯৭টি শয্যায় রোগী ভর্তি ছিল। ফাঁকা ছিল ১৭টি শয্যা, অর্থাৎ ৮৬ শতাংশের বেশি আইসিইউতে রোগী ভর্তি ছিল।
করোনার জন্য নির্ধারিত চারটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে জটিল করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ ফাঁকা না থাকায় অনেক রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।
করোনার জন্য নির্ধারিত যে হাসপাতালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো আবার চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। জটিল রোগীদের জন্য আইসিইউ শয্যা বাড়াতে সরকার চেষ্টা করছে। যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই আইসিইউর ব্যবস্থা করা হচ্ছে
হাবিবুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র ও পরিচালক (এমআইএস)
শীতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করে আসছে সরকার। এরই মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে করোনা শনাক্ত রোগীর হার ঊর্ধ্বমুখী। গত ১৬ নভেম্বর থেকে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দৈনিক ২ হাজারের ওপরে থাকছে। একই সঙ্গে মৃত্যুও বাড়ছে।
শ্বাসতন্ত্রের রোগ কোভিড-১৯-এর জটিল রোগীদের জন্য আইসিইউ ও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়ার সুবিধা বা ভেন্টিলেশন জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, আক্রান্তদের ৪০ শতাংশের উপসর্গ থাকে মৃদু। মাঝারি মাত্রার উপসর্গ থাকে ৪০ শতাংশের। তীব্র উপসর্গ থাকে ১৫ শতাংশের। আর জটিল পরিস্থিতি দেখা যায় বাকি ৫ শতাংশের ক্ষেত্রে। তীব্র উপসর্গ ও জটিল রোগীদের প্রায় সবার এবং মাঝারি উপসর্গ রয়েছে এমন অনেক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। জটিল প্রায় সব রোগীর আইসিইউ শয্যার পাশাপাশি ভেন্টিলেটর দরকার হয়।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র ও পরিচালক (এমআইএস) হাবিবুর রহমান গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, করোনার জন্য নির্ধারিত যে হাসপাতালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো আবার চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। জটিল রোগীদের জন্য আইসিইউ শয্যা বাড়াতে সরকার চেষ্টা করছে। যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই আইসিইউর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
উচ্চমাত্রায় অক্সিজেন সরবরাহের জন্য হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
ঢাকায় করোনার জন্য নির্ধারিত কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের কোনো আইসিইউ শয্যাই গতকাল ফাঁকা ছিল না। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি আইসিইউ শয্যা ফাঁকা ছিল। এ ছাড়া রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের ১৫টি শয্যার ১১টিতে, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালের ১৬টি শয্যার ১০টিতে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬টি আইসিইউ শয্যার ১৪টিতেই রোগী ভর্তি ছিল।
সরকারি কয়েকটি হাসপাতালে যোগাযোগ করেছিলাম। কোনো হাসপাতালে আইসিইউ ফাঁকা নেই। বাধ্য হয়ে মাকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে
মেহেদী হাসান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউর বিভাগীয় প্রধান শাহজাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কুর্মিটোলা হাসপাতালের ১০টি আইসিইউতে সব সময় রোগী ভর্তি থাকছে। একটা শয্যার জন্য একাধিক রোগী অপেক্ষায় থাকছে। ঢাকার বাইরে থেকে করোনার জটিল রোগীদের ঢাকায় পাঠানোর কারণে আইসিইউগুলোতে রোগীর চাপ বেশি। আইসিইউ ফাঁকা না থাকায় অনেক জটিল রোগীকে অন্য হাসপাতালেও পাঠাতে হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানের মা রহমত আরা এখন ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। মেহেদী বলেন, ‘সরকারি কয়েকটি হাসপাতালে যোগাযোগ করেছিলাম। কোনো হাসপাতালে আইসিইউ ফাঁকা নেই। বাধ্য হয়ে মাকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে।’
অবশ্য বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত আইসিইউ শয্যা ফাঁকা থাকছে কম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় করোনা রোগীদের জন্য নয়টি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ রয়েছে ২০৩টি। এর মধ্যে গতকাল রোগী ভর্তি ছিল ১২৯টি শয্যায়। অবশ্য তেজগাঁওয়ের ইমপালস হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা ফাঁকা ছিল ৪৩টি। এই হাসপাতাল বাদে অন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও আইসিইউ শয্যা ফাঁকা নেই বললেই চলে।
রাজধানীর শ্যামলীতে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ১২টি আইসিইউ সুবিধাসহ ৪২ শয্যার করোনা ইউনিট রয়েছে। গতকাল এই হাসপাতালের আইসিইউ এবং সাধারণ কোনো শয্যা ফাঁকা ছিল না। হাসপাতালের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, অধিকাংশ সময় সব শয্যাতে রোগী থাকছে। বিশেষ করে আইসিইউ ফাঁকা থাকছেই না।
ঢাকার হাসপাতালগুলোতে জটিল করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আইসিইউ শয্যা জোগাড়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।
সাধারণ শয্যাতেও রোগী বাড়ছে
করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত ঢাকার নয়টি সরকারি হাসপাতালে সাধারণ শয্যাতেও ভর্তি রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। একসময় সাধারণ শয্যার ৭০ শতাংশের বেশি শয্যা ফাঁকা থাকত। অথচ গতকাল ঢাকার সরকারি হাসপাতালগুলোর ৭৫ শতাংশ শয্যায় রোগী ভর্তি ছিল।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঢাকায় সরকারি হাসপাতালগুলোয় করোনা রোগীদের জন্য সাধারণ শয্যা রয়েছে ২ হাজার ৩৯৭টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৯১টি শয্যায় গতকাল রোগী ভর্তি ছিল। করোনার জন্য নির্ধারিত নয়টি ঢাকার বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেই সাধারণ শয্যায় রোগী ভর্তি বেড়েছে।
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনার জন্য সাধারণ শয্যা রয়েছে ২৭৫টি। গতকাল এই হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিল ৩৫২ জন। অর্থাৎ ধারণক্ষমতার চেয়েও ৭৭ জন রোগী বেশি ভর্তি ছিল এই হাসপাতালে। এর আগে গত সোমবার ধারণক্ষমতার চেয়ে ৬৬ জন বেশি রোগী ভর্তি ছিল।
আইসিইউ শয্যা ফাঁকা থাকছে না, সাধারণ শয্যাতেও রোগী ভর্তি থাকছে। দেশে আবার করোনা রোগী বাড়তে শুরু করেছে, এটি তারই ইঙ্গিত। এত দিনেও আইসিইউ শয্যা বাড়ানো সম্ভব হয়নি, এটি দুঃখজনক। সরকার করোনার জন্য নির্ধারিত যেসব হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছিল, সেগুলো আবার দ্রুত চালু করতে হবে
আবু জামিল ফয়সাল, জনস্বাস্থ্যবিদ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য
ঢাকার বাইরে রোগীর চাপ কম
করোনার চিকিৎসার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর বাদে সারা দেশে এখন সাধারণ শয্যা আছে ৭ হাজার ১৬৪টি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এসব হাসপাতালে গতকাল ভর্তি ছিলেন ৫৫৬ জন। খালি ছিল ৬ হাজার ৬০৮টি শয্যা। অর্থাৎ ৯২ শতাংশ শয্যা খালি পড়ে ছিল। আবার নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) রয়েছে ২১৯টি। গতকাল আইসিইউতে ছিলেন ৮৩ জন। অর্থাৎ আইসিইউর ৬২ শতাংশ শয্যা ফাঁকা ছিল।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল পর্যন্ত দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৪ লাখ ৬৭ হাজার ২২৫ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৮৩ হাজার ২২৪ জন আর মারা গেছেন ৬ হাজার ৬৭৫ জন। চিকিৎসাধীন রোগী আছেন ৭৭ হাজার ৩২৬ জন।
জনস্বাস্থ্যবিদ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য আবু জামিল ফয়সাল প্রথম আলোকে বলেন, আইসিইউ শয্যা ফাঁকা থাকছে না, সাধারণ শয্যাতেও রোগী ভর্তি থাকছে। দেশে আবার করোনা রোগী বাড়তে শুরু করেছে, এটি তারই ইঙ্গিত। এত দিনেও আইসিইউ শয্যা বাড়ানো সম্ভব হয়নি, এটি দুঃখজনক। সরকার করোনার জন্য নির্ধারিত যেসব হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছিল, সেগুলো আবার দ্রুত চালু করতে হবে।
লাইনচ্যুত ট্রেনের মতো রাজনীতিও লক্ষ্যচ্যুত
পঙ্কজ ভট্টাচার্য ঐক্য ন্যাপের সভাপতি ও সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ৮১ বছর বয়সী এই রাজনীতিক বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমলের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে জেল খেটেছেন। সমাজ ও রাজনীতির হালচাল নিয়ে তিনি কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সোহরাব হাসান।
- আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যে আদর্শের কথা বলে, তৃণমূলের নেতারা তা পালন করেন না। সেখানে দেখা যায়, টাকা দিয়ে পদপদবি কেনা যায়। জামায়াতের লোকজনও আওয়ামী লীগে ঢুকে পড়েছে। দুর্নীতিবাজেরা ঢুকে পড়েছে।
- বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমলে যত অর্জন হয়েছে, সব রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল নয়। সামাজিক শক্তিরও বিরাট ভূমিকা ছিল। ছাত্রদের ভূমিকা ছিল। শুধু রাজনীতি দিয়ে সমাজ বদলানো যাবে না।
আপনারা বলেন, পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরই সব অধোগতির শুরু। কিন্তু তিয়াত্তরের নির্বাচনেও তো কারচুপি হয়েছে।
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: তিয়াত্তরের নির্বাচনেও কারচুপি হয়েছে। ১২-১৩টি আসনে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আসনে ন্যাপের বিজয়ী প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলের অনেকে মনোনয়নপত্রও জমা দিতে পারেননি। তবে সেই নির্বাচনে কারচুপি না হলেও আওয়ামী লীগই জয়ী হতো। ক্ষমতার পরিবর্তন হতো না।
তখনকার রাজনীতির সঙ্গে এখনকার ফারাকটা কোথায়?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: একাত্তরে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র পরিচালনায় চার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ৯ মাসের মধ্যে সংবিধান রচিত হয়েছিল। সেই সংবিধানে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ছিল না। এরপরও বলব, এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান ছিল। এরপর সংবিধান অনেকবার কাটাছেঁড়া করা হলো। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা আছে। আমাদেরও ব্যর্থতা আছে। আশির দশকে, নব্বইয়ের দশকে আওয়ামী লীগ যেখানে ছিল, সেখানে নেই।
আওয়ামী লীগের আপসটা কী?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: তারা বলছে সংবিধানে চার মূল নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। আবার রাষ্ট্রধর্মও রেখে দিয়েছে। দুটি একসঙ্গে চলতে পারে না। তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ করার কথা বলছে। আবার হেফাজতে ইসলামের পরামর্শে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করেছে। আওয়ামী লীগ মনে করছে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে এসব করতে হবে। জনগণের ওপর আস্থা কমে গেলে এ অবস্থা হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যে আদর্শের কথা বলে, তৃণমূলের নেতারা তা পালন করেন না। সেখানে দেখা যায়, টাকা দিয়ে পদপদবি কেনা যায়। জামায়াতের লোকজনও আওয়ামী লীগে ঢুকে পড়েছে। দুর্নীতিবাজেরা ঢুকে পড়েছে।
স্বাধীনতার পর আপনারা (ন্যাপ-সিপিবি) আওয়ামী লীগের সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন কেন?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও পাকিস্তানকে পরাস্ত করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আওয়ামী লীগ ও আমাদের চিন্তাধারার মিল ছিল। ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সিপিবি নেতা মণি সিংহ ও খোকা রায়ের বৈঠকে হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন আমরা একসঙ্গে করেছি। যদিও ঐক্যের বিষয়ে মতভেদ ছিল। স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক বাস্তবতা আমাদের ওই দিকে ঠেলে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সমর্থন ছিল। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিরোধিতা এবং উসকানি ছিল। তখন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখাই মুখ্য ছিল। এরপরও মনে করি, আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিশে না গিয়ে গঠনমূলক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল।
একদা বাম রাজনীতি করতেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল আপনাদের মূল স্লোগান। সেখান থেকে সরে এলেন কেন?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমরা উপলব্ধি করলাম, অন্য কোনো দেশের মডেল বা মতাদর্শের রাজনীতি দিয়ে এগোনো যাবে না। বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী রাজনীতি করতে হবে। এ কারণেই প্রচলিত বাম ধারা থেকে বেরিয়ে এসে মানবতাবাদী রাজনীতি করেছি।
একসময় চীনপন্থীদের সম্পর্কে দল ভাঙার অভিযোগ ছিল। এখন মস্কোপন্থীরাও নানা ভাগে বিভক্ত। এর পেছনে আদর্শ না নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব কাজ করেছে?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: এখানে আদর্শ গৌণ। মূলত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমি নতুন করে ঐক্যের চেষ্টা করছি। গণতান্ত্রিক পার্টি, ন্যাপ মোজাফ্ফরের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। ১৪ দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তাঁদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের অনেকেই একমত যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বাইরে থেকে একটা চাপ সৃষ্টি করা দরকার, যাতে রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে দূরে সরে না যায়। আমরা সমাজের ন্যায়–নীতিনিষ্ঠ মানুষগুলোকে একত্র করতে চাই। গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির উদ্বোধন চাই।
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রত্যয় ছিল গণতন্ত্র। সেই গণতন্ত্রের এখন কী অবস্থা?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: এটি একটি বড় বিষয়। পাকিস্তান আমলে যে গণতন্ত্র ছিল, যে নির্বাচন ছিল, যাতে জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটেছে; এখন তো সেই নির্বাচন নেই। ১৯৭০ সালের নির্বাচনই তো দেশকে স্বাধীনতার পথে নিয়ে গেল। গণতন্ত্র এখন মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, মানুষের অন্তরে নেই। বর্তমানে গণতন্ত্র হলো প্রশাসনিক গণতন্ত্র, আমলাতান্ত্রিক গণতন্ত্র।
সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে পাকিস্তান আমল থেকে আপনারা আন্দোলন করেছেন। আন্দোলন করে সামরিক শাসককে পদত্যাগে বাধ্য করেছেন। যার লক্ষ্য ছিল সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন। এখন সেই পরিবেশ কি আছে?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: মানুষ আস্থা হারিয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন একের পর এক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেছে। এই ব্যবস্থা না বদলালে মানুষকে নির্বাচনমুখী করা যাবে না। ভোটারশূন্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তাতে জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটছে না। আমরা যদি সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। গণতন্ত্রের যে ক্ষীণধারা চলছে, তা–ও হয়তো হারিয়ে যাবে।
নির্বাচনী ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়ল, এ জন্য কাকে বেশি দায়ী করবেন? সরকার না নির্বাচন কমিশন?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: নির্বাচন কমিশন সিংহভাগ দায়ী। এই কমিশন হলো মেরুদণ্ডহীন। ১০ শতাংশ ভোটার উপস্থিত হলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। সরকারও সন্তুষ্ট। সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তারা এটি করতে পেরেছে।
২৩ বছর আগে পার্বত্য চুক্তি সই হয়েছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ কী?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া বাঙালি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য। সরকার বলছে তিন ভাগের দুই ভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বলছে, তিন ভাগের এক ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, বাঙালিদের পাশাপাশি পাহাড়ি ও সমতলের জাতিগোষ্ঠী থেকেও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন চালানো গৌরবের কথা নয়। সমতলের জাতিগোষ্ঠীর লোকজনও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসন নির্বিকার। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়। বাস্তবায়ন হয় না। গাইবান্ধায় তিনজন সাঁওতালের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলো। রাষ্ট্র দায় নিল না। যাঁরা উচ্ছেদ হলেন, তাঁরা পৈতৃক সম্পত্তিও ফেরত পেলেন না। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সমতলের জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের কথা বলেছিল। বাস্তবায়িত হয়নি।
করোনাকালে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: করোনার কারণে চাকরি হারানো, জীবিকা হারানো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্যের হার বাড়ছে। সংকট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা আছে। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর নির্দেশ পৌঁছায় না। আজ স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, সড়ক বিভাগের অবস্থা খুবই নাজুক। সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট যে রায় দিলেন, তা–ও বাস্তবায়িত হয় না।
রাজনীতির পাশাপাশি আপনি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত। সেটি কি রাজনৈতিক হতাশা থেকে?
পঙ্কজ ভট্টাচার্য: ১৯৯৬ সালে এসে দেখলাম রাজনীতি বৃহত্তর মানুষের জীবনকে তেমন স্পর্শ করতে পারছে না। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ নিজেদের মতো প্রতিবাদ করছে। এই সামাজিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আমরা সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অজয় রায়ের মতো মানুষ এর সঙ্গে ছিলেন। এর মাধ্যমে আমরা অসাম্প্রদায়িক শক্তির সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছিলাম। অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলাম। ২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি হলো। ডাকসুর নির্বাচনেও নতুন শক্তির উত্থান দেখলাম। সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ নামে একটি সংগঠন নির্বাচনে জয়ী হলো। প্রচলিত ছাত্রসংগঠনগুলো সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন পেল না। এরপর কিশোর-তরুণেরা নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করল। এ কারণে এখনো আশাবাদ আছে। নতুন প্রজন্ম জাগবে। সবাইকে নিয়েই পরিবর্তন আনতে হবে।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমলে যত অর্জন হয়েছে, সব রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল নয়। সামাজিক শক্তিরও বিরাট ভূমিকা ছিল। ছাত্রদের ভূমিকা ছিল। শুধু রাজনীতি দিয়ে সমাজ বদলানো যাবে না।